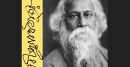পাকিস্তানিদের চোখে নজরুল
প্রকাশিত হয়েছে : ১১ মার্চ ২০১৭, ১১:৫৭ অপরাহ্ণ
 সুরমা নিউজঃ বাংলা সাহিত্যে ধর্মনিরপেক্ষতার প্রতীক কাজী নজরুল ইসলাম। তাঁর সাহিত্যে এককভাবে কোনো বিশেষ ধর্মের প্রভাব ছিল না। ব্যক্তিজীবনেও নজরুলের মধ্যে ধর্মীয় উদারতা লক্ষণীয়। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের আগে তাঁকে কোনো বিশেষ ধর্ম-গোষ্ঠীর কবি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়নি। ‘তিনি বিশেষ কোনো সম্প্রদায়ের কবি’—নজরুলকে নিয়ে এই দৃষ্টিভঙ্গি এসেছে ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র পাকিস্তান প্রতিষ্ঠারও বেশ পরে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরপর শাসকগোষ্ঠীর কাছে বিদ্রোহী কবির মূল্যায়ন ছিল ভিন্ন রকম।
সুরমা নিউজঃ বাংলা সাহিত্যে ধর্মনিরপেক্ষতার প্রতীক কাজী নজরুল ইসলাম। তাঁর সাহিত্যে এককভাবে কোনো বিশেষ ধর্মের প্রভাব ছিল না। ব্যক্তিজীবনেও নজরুলের মধ্যে ধর্মীয় উদারতা লক্ষণীয়। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের আগে তাঁকে কোনো বিশেষ ধর্ম-গোষ্ঠীর কবি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়নি। ‘তিনি বিশেষ কোনো সম্প্রদায়ের কবি’—নজরুলকে নিয়ে এই দৃষ্টিভঙ্গি এসেছে ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র পাকিস্তান প্রতিষ্ঠারও বেশ পরে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরপর শাসকগোষ্ঠীর কাছে বিদ্রোহী কবির মূল্যায়ন ছিল ভিন্ন রকম।
১৯৪৭-এর আগস্টে যখন পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম হয়, কাজী নজরুল ইসলাম সে সময় অসুস্থ অবস্থায় পার্শ্ববর্তী ভারতে অবস্থান করছিলেন। বেশ কিছু উন্নতমানের ইসলামি কবিতা ও গান রচনা করলেও ইসলাম ধর্মের অনুশাসনের বিষয়ে খুব একটা যত্নবান ছিলেন নজরুল—এমন প্রমাণ মেলে না। তিনি বিয়ে করেছিলেন হিন্দু নারীকে, ফলে তাঁর পরিবারে খুব নিষ্ঠভাবে ধর্মের চর্চা ছিল—এটা বলা কঠিন। অন্যদিকে, কবি প্রথমে কংগ্রেস এবং পরে কমিউনিস্ট রাজনীতিতে যুক্ত ছিলেন। ১৯২৬ সালে পূর্ববঙ্গ থেকে কেন্দ্রীয় আইনসভার উচ্চ পরিষদ নির্বাচনে কংগ্রেসের সমর্থন-প্রত্যাশী হয়ে মুসলমানদের জন্য সংরক্ষিত আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাও করেন। স্বভাবত, এ দুই কারণে স্বাধীনতার পরপর পাকিস্তানের নীতিনির্ধারকেরা নজরুলকে খুব একটা পছন্দ করেননি। উল্লেখ করা যেতে পারে, এ সময়ের প্রায় সব জ্যেষ্ঠ আমলা ছিলেন অবাঙালি। ফলে নজরুল এবং তাঁর সাহিত্যকর্ম সম্পর্কে তাঁদের সম্যক ধারণা না থাকা অসম্ভব নয়।
কিন্তু পরবর্তীকালে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে কাজী নজরুল ইসলামকে দাঁড় করানোর অপচেষ্টা করেছে। রবীন্দ্রনাথের প্রভাব ও জনপ্রিয়তাকে খাটো বা প্রতিহত করার জন্য পাকিস্তানিদের কাছে এ সময় আদরণীয় হয়ে ওঠেন নজরুল। বলা ভালো, এ সময় নজরুলের ইসলামি গান-কবিতাসহ তাঁর বিচিত্র রকম সৃষ্টির চর্চাও শুরু হয় জোরেশোরে। একই সঙ্গে আরম্ভ হয় নজরুলকে ‘সাচ্চা মুসলমান’ হিসেবে উপস্থাপনের প্রয়াস।
তবে পাকিস্তান সৃষ্টির প্রথম দিকে কীভাবে অবজ্ঞা করা হয়েছিল নজরুলকে, অবাঙালি পাকিস্তানি আমলাদের কাছে কেমনভাবে নিগৃহীত হয়েছিলেন তিনি, সেটি বোঝা যাবে নিচের সরকারি নথিতে থাকা দুই ঘটনা থেকে। ইংরেজি ভাষায় দুটি ঘটনাই লেখা রয়েছে সরকারি নথিতে। বর্তমানে নথিগুলো জাতীয় মহাফেজখানায় সংরক্ষিত আছে।
প্রথম ঘটনা
১৯৫০ সালের ৩ আগস্ট স্বরাষ্ট্র (রাজনৈতিক) বিভাগ ‘ফুলার রোড’-এর নাম ‘কবি নজরুল অ্যাভিনিউ’-এ পরিবর্তন করার একটি প্রস্তাব নোটশিটের মাধ্যমে উত্থাপন করে। নোটশিট থেকে বোঝা যায়, প্রস্তাবটি সিবি অ্যান্ড আই (কনস্ট্রাকশন, বিল্ডিং অ্যান্ড ইরিগেশন) বিভাগ থেকে ১৯৫০-এর জুলাই বা তারও আগে উত্থাপন করা হয়। সিবি অ্যান্ড আই বিভাগের কোনো নথি নোটশিটে সংযুক্ত না থাকায় বোঝা যায় না যে কেন এবং কখন এই নাম পরিবর্তনের উদ্যোগ নেওয়া হয়। নোটশিটের প্রথমেই স্বরাষ্ট্র বিভাগের সূত্রপাতকারী কর্মকর্তা নিচের কারণগুলো উল্লেখ করে ফুলার রোডের নাম নজরুল অ্যাভিনিউ হিসেবে পরিবর্তনের বিরোধিতা করেন:
১. কবি এখনো বেঁচে আছেন।
২. তিনি কখনো পাকিস্তানে আসা এবং এখানে বসবাসের ইচ্ছা প্রকাশ করেননি। এখনো তিনি আধা হিন্দু (গুজবে জানা যায়) জীবনযাপন-পদ্ধতি অব্যাহত রেখেছেন।
৩. যদি প্রস্তাবটি কার্যকর করা হয়, তবে সংবাদমাধ্যমে আলোড়ন সৃষ্টির সুযোগ বা যুক্তি সৃষ্টি হবে এই কারণে যে, একটি ইসলামিক রাষ্ট্র এমন একজন মানুষকে সম্মানিত করেছে, যে মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও নিজের ইচ্ছায় অ-ইসলামিক জীবনযাপন বেছে নিয়েছে।’
এরপর স্বরাষ্ট্র বিভাগের পরবর্তী জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা ১৯৫০-এর ৩ সেপ্টেম্বর নিচের মতামত দেন:
‘যদি ফুলার রোডের নাম পরিবর্তন করা হয়, তবে তা হওয়া উচিত এমন একজনের নামে, যিনি মুসলমান ও পাকিস্তানের প্রীতি ও ভালোবাসা অর্জন করেছেন। কবি হিসেবে তিনি [নজরুল] যাঁদের প্রীতি অর্জন করেছেন, তাঁরা ব্যতীত এই প্রদেশের সাধারণ মানুষ তাঁর [নজরুল] প্রতি শ্রদ্ধাশীল নয়। তাই প্রস্তাবটিতে স্বরাষ্ট্র বিভাগ সম্মতি দিতে পারে না। যদি তাঁর নাম এই প্রদেশের কোনো কিছুর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করতে হয়, তবে অধিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের নাম বিবেচনায় আনার পর তা করা উচিত।’
নোটশিটের শেষে ৩ অক্টোবর পূর্ব বাংলা সরকারের উপসচিব ডি কে পাওয়ার নিম্নোক্ত মতামত দেন:
‘সড়কের নাম পরিবর্তন অনুমোদনের জন্য স্বরাষ্ট্র (রাজনৈতিক) বিভাগ যোগ্য কর্তৃপক্ষ নয়। যত দূর জানি, এই ক্ষমতা যে সড়কের নাম পরিবর্তনের প্রস্তাব করা হয়েছে, তার নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের ওপর এককভাবে ন্যস্ত—সাধারণভাবে পৌরসভা। কিন্তু এইচ অ্যান্ড এলএসজি বিভাগের পাতা ৩-এ প্রদত্ত নোট দেখে স্পষ্টত প্রতীয়মান হয় যে এই বিষয়টি সিবি অ্যান্ড আই বিভাগের আওতাধীন। যাহোক, যেহেতু সিবি অ্যান্ড আই বিভাগ আমাদের মতামত চেয়েছে, তাই তাদের বিবেচনার জন্য রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে আমাদের সুপারিশ দাখিল করলাম।
‘অস্বীকার করার উপায় নেই যে, কাজী নজরুল ইসলাম এ সময়ের সবচেয়ে খ্যাতিমান মুসলিম কবি, যিনি বাংলায় [সাহিত্য] রচনা করেছেন। তাঁর জীবনের কিছু সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য আছে, যা তাঁর নামে সড়ক নামকরণের বিরুদ্ধে হাজির করা যায়। পাকিস্তানের সঙ্গে তাঁর কোনো অন্তরঙ্গ সম্পৃক্ততা নেই। উপরন্তু তিনি বসবাস করছেন ভারতে। তথাপি সম্ভবত এই সরকার তাঁর জন্য কিছু ভাতা বরাদ্দ করেছে। আমি অনুমান করি, কিছু বছর ধরে তিনি মানসিকভাবে ভারসাম্যহীন অবস্থায় আছেন। আমার ধারণা, মানসিক ভারসাম্য হারানোর আগে তিনি এক হিন্দু নারীকে বিয়ে করেছেন এবং আংশিক হলেও ইসলামি জীবনযাপন পরিত্যাগ করেছেন। তাই তাঁর নামে সড়কের নামকরণ হলে, কোনো বিশেষ গোষ্ঠী থেকে এই অজুহাতে বাধা আসতে পারে যে তিনি পাকিস্তান নামের ইসলামি রাষ্ট্র থেকে এই সম্মান পাওয়ার যোগ্য নন, যেহেতু পাকিস্তানের কীর্তিমান সন্তানদের এখনো স্মরণীয় করা হয়নি। তাই এই পরিকল্পনাটি পরিত্যাগ করাই হবে অধিক নিরাপদ—এটাই আমাদের সুপারিশ।
‘যাহোক, যদি সম্মিলিত মতামত প্রস্তাবের পক্ষে যায়, তবে রাজনৈতিক নয়, বরং ভাষাতত্ত্বের দৃষ্টিকোণ থেকে আমি নিচের মন্তব্যটি পেশ করব। “নজরুল ইসলাম” নামটির একটি অর্থ (অন্যান্য মুসলমান নামের মতো) ও ধর্মীয় তাৎপর্য আছে। তাই এর অংশ মাত্র—যেভাবে প্রস্তাব করা হয়েছে—ব্যবহার করা আপত্তিকর মনে হবে। আমি আরবি-বিশারদ নই, তবে মনে হয়, আমি সঠিক যদি বলি “নজরুল” অর্থ “দৃষ্টিশক্তি”, “দৃষ্টিগোচরতা” এবং এর সঙ্গে সামান্য ব্যাপ্তি ঘটালে মানে দাঁড়ায় “ইসলামের শোভাময় দৃষ্টিগোচরতা” বা “মহিমা”। “উল” শব্দের পরপরই থেমে যাওয়া কিছুটা অস্বাভাবিক হবে এবং অ্যাভিনিউয়ের সঙ্গে সংযোগ ঘটালে তা আরও উদ্ভট মনে হবে, যদি না কেউ ভুলে যায় যে এই নামের একটি স্বকীয় অর্থ আছে।
‘শেষে আমি এই কথাই বলব, যদি সড়ক নামকরণের মাধ্যমে আমরা জাতীয় বীরদের স্মরণীয় করতে চাই, তবে আমাদের সেসব সড়ক নির্বাচিত করতে হবে, যেগুলোর ইতিমধ্যে নামকরণ করা হয়েছে এমন ব্যক্তিদের নামে, যাঁদের পাকিস্তানে স্মরণীয় করা উচিত হবে না।
‘আমি ঢাকা শহরে “সুভাষ অ্যাভিনিউ”-এর চিন্তা করছি এবং সম্ভবত অন্যান্য পৌরসভায়ও এ ধরনের আরও অনেকে আছেন, বিশেষ করে দেশভাগের আগে যে এলাকাগুলোতে অমুসলিমদের সংখ্যাধিক্য ছিল।’ এরপর নথিটি বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং ১৯৫০ সালের ৮ নভেম্বর মহাফেজখানায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়।
দ্বিতীয় ঘটনা
১৯৫১ সালের প্রথমার্ধে নজরুল ইসলামের সাহায্যার্থে দিনাজপুরে ‘নজরুল এইড কমিটি’ একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। এই অনুষ্ঠান থেকে ১ হাজার ৮৯ টাকা ৮ আনা সংগ্রহ হয়। কমিটি সংগৃহীত টাকা কলকাতায় বসবাসরত কবিকে পাঠানোর কোনো বৈধ পথ না পেয়ে দিনাজপুরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের (ডিএম) শরণাপন্ন হয়। ১৯৫১ সালের ২৭ জুন ডিএম পত্র মারফত পূর্ব বাংলা সরকারের স্বরাষ্ট্র (রাজনৈতিক) বিভাগকে বিষয়টি অবহিত করেন। ডিএম পত্রে উল্লেখ করেন যে বর্ণিত অর্থ কমিটির সভাপতির নিকট গচ্ছিত রয়েছে। মুদ্রা বিনিময়ের জটিলতার কারণে তা কবির কাছে পাঠানো সম্ভব হচ্ছে না। স্বরাষ্ট্র বিভাগকে যত দ্রুত সম্ভব কবির কাছে অর্থ পাঠানোর ব্যবস্থা নিতে অনুরোধ করেন তিনি।
এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য স্বরাষ্ট্র বিভাগ ১১ জুলাই একটি নোটশিটের সূত্রপাত করে। সূত্রপাতকারী কর্মকর্তা উল্লেখ করেন:
‘এটি বোঝা গেল না যে হিন্দুস্থানের একজন বিশেষ ব্যক্তির ত্রাণের জন্য কেন পাকিস্তানিরা অর্থ প্রেরণ করবে, যখন শত শত মুসলিম পিয়ন এর চেয়েও অত্যধিক দুর্বিষহ অবস্থায় তাদের দিন কাটাচ্ছে। ডিএমের পত্রটি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের জন্য অর্থনৈতিক বিভাগে প্রেরণ করা যেতে পারে এবং ডিএমকে অবহিত করা যেতে পারে।’
এরপর প্রায় পাঁচ মাস গত হয়ে গেলেও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে এ বিষয়ে কোনো উত্তর আসেনি। ইতিমধ্যে কমিটি বা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট দিনাজপুরে সেন্ট্রাল ব্যাংক অব ইন্ডিয়ার স্থানীয় সাব-এজেন্টের সঙ্গে যোগাযোগ করলে তারা জানায়, কবির কলকাতার ঠিকানা দিলে তাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে এই টাকা কবিকে পৌঁছে দেওয়া যাবে। ২৭ নভেম্বর ডিএম আবারও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে চিঠি লিখে কবির ঠিকানা জানতে চান। ঠিকানা না পাওয়া গেলে অগত্যা এই টাকা কী করা হবে, চিঠিতে সেই পরামর্শও চাওয়া হয়।
আগের নোটশিট ও দিনাজপুরের ডিএমের দ্বিতীয় চিঠিতে প্রদত্ত প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে স্বরাষ্ট্র বিভাগ ৮ ডিসেম্বর ১৯৫১ সালে কলকাতার ডেপুটি হাইকমিশনারকে একটি চিঠি দেয়। ডেপুটি হাইকমিশনার কবির ঠিকানা (১৬ রাজেন্দ্র লাল স্ট্রিট, টপ ফ্লোর, কলকাতা-৬) সংগ্রহ করে ২৮ ডিসেম্বর জানিয়ে দেয় স্বরাষ্ট্র বিভাগকে। তারপর ১৯৫২-এর জানুয়ারি মাসে স্বরাষ্ট্র বিভাগ দিনাজপুরের ডিএমকে কবির ঠিকানা দেয়। এরপর কী ঘটেছিল, তার কোনো উল্লেখ নথিতে আর পাওয়া যায় না।